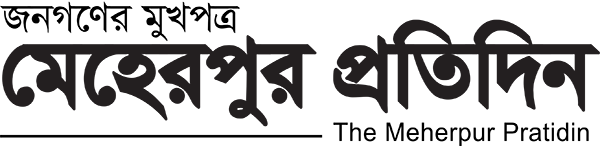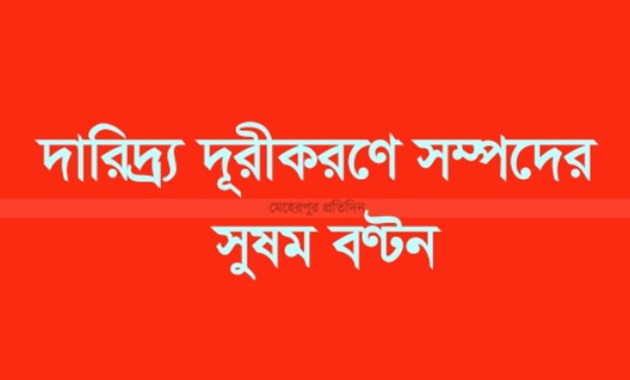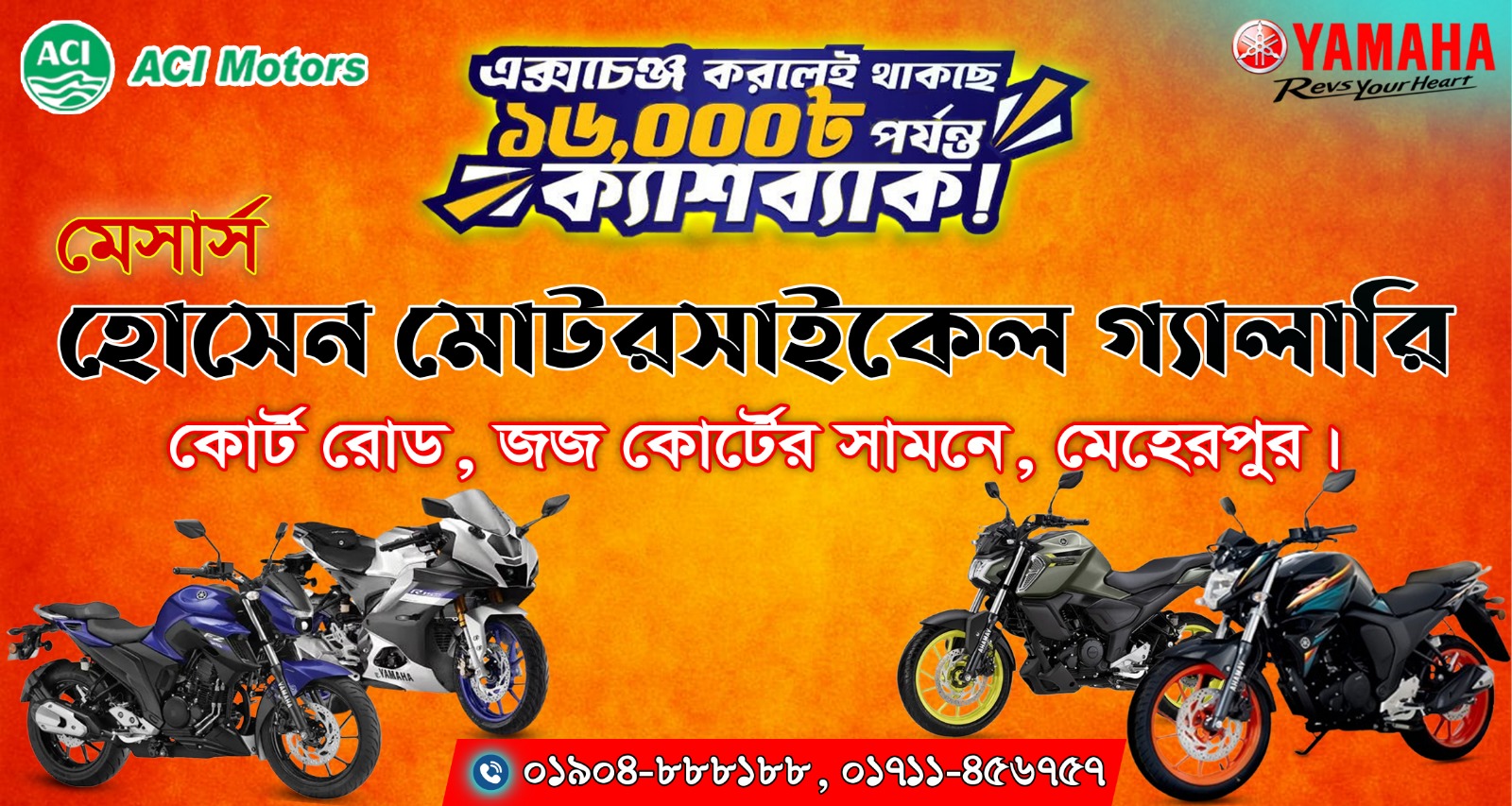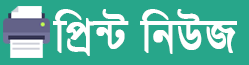
দারিদ্র্য এক নির্মম অভিশাপ। এ অভিশাপ মানুষকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। সমাজ-সভ্যতাকে এগিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে পিছিয়ে দেয়। এটা মানবতাকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে দিতে পারে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে, ক্ষুধার নির্মম যাতনায় ও অভাবের অনলে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে ন্যায়-অন্যায় বিস্মৃত মানবকুল পাপ-পঙ্কিলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে নিজের অজান্তেই আত্মবিধ্বংসী পথে অগ্রসর হয়। দারিদ্র্যের এ নির্মম জ্বালায় মানবতাবোধ লোপ পায়, হিংস্রতার প্রসার ঘটে, অন্যায়-অবিচার বিস্তৃত হয়। নারী তার পরম যত্নে লালিত সতীত্বকে বিলিয়ে দিতে পারে, মানুষ তার প্রিয় সন্তানকে বিক্রি করে দিতে পারে, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করতেও দ্বিধা করে না। অন্যভাবে বললে, দারিদ্র্য হলো রক্তশূন্যতার সদৃশ। রক্তশূন্যতা দেখা দিলে মানুষের দেহ নানা দুরারোগ্য ব্যাধির আবাসে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে সম্পদের স্বল্পতা থাকলে মানুষের জীবনও অচল হয়ে পড়ে।
দারিদ্র্য দূরীকরণে সম্পদের সুষম বণ্টন অত্যন্ত জরুরি, কারণ এটি অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করে এবং দেশের সম্পদকে কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া থেকে বিরত রাখে। সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ পায় এবং অর্থনৈতিকভাবে উন্নত জীবন লাভ করে। আবার, যখন সম্পদ অসমভাবে বণ্টিত হয়, তখন সমাজে ধনী ও গরিবের মধ্যে বড়ো ব্যবধান গড়ে ওঠে। এ বৈষম্য কমলে সমাজে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে, সকলের জন্য ন্যূনতম সুযোগের সমতা তৈরি হয় এবং কেউ বঞ্চিত হয় না। আবার, মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হলে তা অপচয়ের আশঙ্কা থাকে। অল্প কিছু মানুষের হাতে যেন সম্পদ পুঞ্জীভূত হতে না পারে সে ব্যাপারে রাষ্ট্র কম-বেশি পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো এমন নীতি গ্রহণ করতে পারে, যাতে সম্পদের অসম বণ্টন রোধ করা যায় এবং সবাই যেন তাদের মৌলিক চাহিদাটুকু মেটাতে পারে। দরিদ্র মানুষের হাতে পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকলে তারা দারিদ্র্যের মধ্যেই ঘুরপাক খায়। সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।
‘দারিদ্র্য’ ও ‘বাংলাদেশ’ শব্দদ্বয় একত্রে বিসদৃশ লাগে। কারণ বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনার দেশ। সম্পদে ভরপুর দেশটির স্বীকৃতি দিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সময়ে ছুটে আসা পর্যটক, বিশেষজ্ঞ, জ্ঞানী-গুণী ও ভূ-তত্ত্ববিদরা। অথচ বর্তমানে আমাদের দেশে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা চার কোটি ৬৭ লাখ ৮৯ হাজার ৭৭২ জন, যা শতকরা বিচারে ৩১ দশমিক পাঁচ ভাগ; এবং অতি দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দুই কোটি ৬০ লাখ ৬৫ হাজার ১৭১ জন, যা শতকরা ১৭ দশমিক ছয় ভাগ।
দারিদ্র্যের অর্থ হচ্ছে দরিদ্র অবস্থা, অভাব ও দীনতা। দারিদ্র্য বলতে এমন ব্যক্তি বা দেশকে বোঝায়, যার সামান্য সম্পদ ও অল্প আয় রয়েছে, যা দ্বারা ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ। ডেলটুসিং বলেন, “মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতাই হলো দারিদ্র্য।” থিওডরসনের মতে, “দারিদ্র্য হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক উপোস।”
কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দারিদ্র্য কমাতে কৃষি ও শিল্পকারখানার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানো দরকার। প্রতিবছর হাজার হাজার তরুণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষিত হয়ে বের হচ্ছে। একই সাথে কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থার অভাবে দেশে বেকারত্ব বাড়ছে। এমনকি বাংলাদেশে শ্রমিকদের মজুরি প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। শুধু কৃষি নয়, শিল্প ও অন্যান্য খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন, যাতে সমাজের সকল স্তরের মানুষ জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পায়। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও সর্বোচ্চ চেষ্টা করে দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারেন। দারিদ্র্য কমাতে সবার আগে খাদ্য নিরাপত্তায় জোর দেওয়া প্রয়োজন। আবাদি জমি বাড়াতে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি পরিচালনা, কৃষি যন্ত্রপাতির আধুনিকায়ন, শিল্পনগরীগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন, উপজেলা পর্যায়ে বিশেষায়িত কোল্ড স্টোরেজ প্রতিষ্ঠা, উপজেলা কৃষি উন্নয়ন কর্মকর্তাদের জবাবদিহি ও কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি করা গেলে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।
যদি ইসলামী সমাজব্যবস্থার কথা ভাবি, তাহলে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ধনীরা তাদের সম্পদের কিছু অংশ গরিবদের দান করে, যা সম্পদের সুষম বণ্টনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলাম কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য আর্থিক সাহায্যের বিধান রেখেছে। একটি সুখী, সুন্দর ও উন্নত সামাজিক পরিবেশ গঠনে ধনাঢ্য মুসলমানদের অবশ্যই তাদের নিসাব পরিমাণ সম্পদের একটি নির্ধারিত অংশ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের দুর্দশা মোচনের জন্য ব্যয় করতে হবে। ফলে কেবল অসহায় ও দুস্থ মানবতার কল্যাণই হবে না; বরং সমাজে আয়বণ্টনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য হ্রাস পাবে। পবিত্র কোরআনে সূরা আল-হাশরের সাত নম্বর আয়াতে ধনসম্পদ বণ্টনের মূলনীতি সম্পর্কে ঘোষণা হয়েছে “যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান, কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।”
নৈতিকতাহীন নেতৃত্বের ফলে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন বাধাগ্রস্ত হয়। এই বাস্তবতার পটভূমিতে যাকাতকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কার্যকর মাধ্যম হিসেবে দেখা হচ্ছে। ইসলামী সামাজিক অর্থায়নের ধারণা শুধু দারিদ্র্য দূরীকরণেই নয়, বরং বৈষম্য কমিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতি গড়তেও ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্বজুড়ে যাকাতের নীতিমালা সম্পদ পুনর্বণ্টনের একটি স্বীকৃত ও টেকসই উপায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যাকাত সম্পদের সুষম বণ্টনের অপরিহার্যতা ও মানবিক দায়িত্ববোধকে একসঙ্গে তুলে ধরে।
আধুনিক সমাজে সাফল্যের মানদণ্ড হয়ে উঠেছে ভোগের ক্ষমতা; ফলে সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রায়শই উপেক্ষিত হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে অতীতে বহু আন্দোলন ও ত্যাগ স্বীকারের পরও অসাম্য আজও টিকে আছে। এর মূল কারণ ন্যায্য সম্পদ বণ্টনের ঘাটতি। তাই বৈষম্য দূর করে সামাজিক সাম্য ও মানবিক মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে যাকাতভিত্তিক ন্যায়সংগত অর্থনৈতিক কাঠামো বিনির্মাণ মনোযোগের দাবিদার।
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার বেশ আলোচিত হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশ অচিরেই ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দেশ হতে যাচ্ছে। অর্থনীতির আকার বড়ো হচ্ছে, অগ্রগতির পথে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অতিদরিদ্র মানুষের সংখ্যা যদি বেড়ে যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী যদি বঞ্চিত থেকে যায়, তাহলে ওই অগ্রগতি আদৌ অগ্রগতি নয়। আবার, কেবল শহরকেন্দ্রিক উন্নয়ন হলে তা সুষম উন্নয়ন হবে না। পল্লী উন্নয়ন মূলত উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্পদের সুষম বণ্টন ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনমান উন্নয়নের জন্য এক পরিকল্পিত পরিবর্তন। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের চাবিকাঠি হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ ও গ্রামীণ দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন, ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। অনেক উন্নয়নশীল দেশ পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে বেশ সক্রিয়।
১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জিনি সহগ ছিল মাত্র দশমিক ৩৬। জিনি সহগ মূলত আয়-বৈষম্য পরিমাপের একটি পদ্ধতি। তখন বাংলাদেশ দারিদ্র্যকবলিত দেশ হলেও আয়-বৈষম্য ছিল তুলনামূলকভাবে সহনীয়। সেই জিনি সহগ সর্বশেষ ২০১৬ সালে বেড়ে হয়েছে দশমিক ৪৮৩। অর্থাৎ আয়বৈষম্য অনেক বেড়েছে। এখন আমরা ভাবছি, আমাদের চেয়ে বেশি আয়বৈষম্য কোথায়। সারাবিশ্বে অতিধনী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে আমাদের দেশেও। মাথাপিছু আয় ক্রমেই বাড়ছে। করোনাকালে এর মান ছিল আরও ভয়াবহ। সরকারি খানা জরিপের তথ্যমতে, দেশের মোট আয়ের দুই-তৃতীয়াংশের মালিক ওপরের দিকে থাকা এক-তৃতীয়াংশ মানুষ। দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের জন্য এই আকাশচুম্বী ব্যবধান কমাতে হবে।
আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধি তখনই অর্থবহ হয়, যখন এর সুফল ভোগ করে দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের বেশিরভাগ মানুষ। যে প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে ভূমিকা রাখে না, যার সুফল কেবল সমাজের উঁচু স্তরের নাগরিকরা ভোগ করে ওই প্রবৃদ্ধি নিছক সংখ্যা। এ ধরনের প্রবৃদ্ধি কোনোভাবেই কাম্য নয়। বৈষম্য দূর করা না হলে প্রবৃদ্ধি টেকসই হবে না। সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি না হলে বৈষম্য বাড়বে; ধনী হবে আরও ধনী, গরিব হবে আরও গরিব। এমনটি হলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রবাহ বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য ও অসমতা দূর করতে হবে। কেবল সম্পদশালীদের প্রণোদনা-সুবিধা দিয়ে অর্থনীতিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করা সম্ভব নয়। আর্থিক খাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা গেলে প্রবৃদ্ধির সুফল পাবে সবাই।
লেখক: সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা