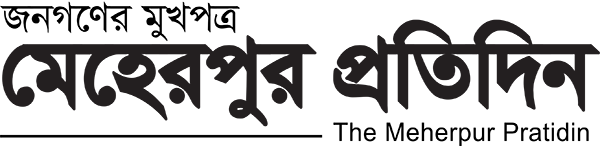
প্রাণঘাতী বজ্রপাত: সচেতনতা ও আগাম সতর্কতা

যেসব ঘটনা মানুষের স্বাভাবিক জীবন ধারাকে ব্যাহত করে মানুষের সম্পদ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে এবং যার জন্য আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যতিক্রমধর্মী প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হয়, তাদের দুর্যোগ বলে। আর প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট দুর্যোগকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা হয়। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো - অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদী ভাঙন, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, ইত্যাদি। বজ্রপাত হলো মেঘের মধ্যে বা মেঘ থেকে ভূমি পর্যন্ত সৃষ্ট বৈদ্যুতিক চার্জের এক ধরনের নির্গমন। যখন মেঘে থাকা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের পরিমাণ বেশি হয়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে বা মেঘের নিচের ভূমির সাথে চার্জের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের ফলে আলোকরশ্মি ও শব্দের সৃষ্টি হয়, যা আমরা আলো ঝলকানি ও বিকট শব্দ হিসেবে শুনতে পাই।
বাংলাদেশে বজ্রপাতের মূল কারণ দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান। কারণ, বাংলাদেশের একদিকে বঙ্গোপসাগর, এরপরই ভারত মহাসাগর। সেখান থেকে গরম আর আর্দ্র বাতাস আসছে। আবার উত্তরে রয়েছে পাহাড়ি এলাকা, কিছু দূরেই হিমালয় রয়েছে, যেখান থেকে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে। এই দুই বাতাসের সংমিশ্রণে বজ্র মেঘ তৈরি হয় এবং এসব মেঘের সাথে মেঘের ঘর্ষণে বজ্রপাত হয়। বাংলাদেশে উত্তরাঞ্চল এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বজ্রপাতপ্রবণ এলাকাগুলোর অন্যতম। গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলে তাপমাত্রা বেশি থাকায় এ পরিস্থিতির তৈরি হয়। আবহাওয়াবিদদের মতে, যেসব এলাকায় গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে সেসব এলাকায় যে মেঘের সৃষ্টি হয়, সেখান থেকেই বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকে। তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়লে বজ্রপাতের সম্ভাবনা ১০ শতাংশ বেড়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ ঘন ঘন বজ্রপাতজনিত দুর্যোগের ঝুঁকিতে রয়েছে। লম্বা গাছ কেটে ফেলায় গ্রামীণ এলাকায় বজ্রপাতের ঝুঁকি আরও বেড়েছে। গাছ কেটে ফেলার ফলে প্রাকৃতিকভাবে বজ্রপাত থেকে সুরক্ষা হ্রাস পেয়েছে ও মানুষের জন্য ঝুঁকি বেড়েছে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, প্রাক-বর্ষাকাল অর্থাৎ, মার্চ থেকে মে মাসে দেশে ৩৮ শতাংশ বজ্রঝড় হয়। বর্ষা অর্থাৎ, জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই চার মাসে ৫১ শতাংশ বজ্রঝড় হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে ৮৪ লাখ বজ্রপাত হয়, যার ৭০ শতাংশই হয় এপ্রিল থেকে জুন মাসে। আবহাওয়াবিদদের পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশে উত্তর, উত্তর পূর্ব এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল সবচেয়ে বেশি বজ্রপাতপ্রবণ। বজ্রপাতে হতাহতের ঘটনা বেশি ঘটে হাওর অঞ্চলে। কেননা এসব অঞ্চলে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে। সে হিসেবে নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট এবং সেইসাথে টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ বজ্রপাতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া, রংপুর, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়ও বজ্রঝড় বেশি হয়। বজ্রপাতে বেশি মৃত্যু হয় কৃষকদের। কারণ, তাঁরা খোলা মাঠে কাজ করেন এবং খালি পায়ে কাজ করেন। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর বজ্রপাতে ১৫০ থেকে ২০০ মানুষ মারা যায় যাদের বেশিরভাগই কৃষক। সেইসঙ্গে অনেক গবাদি পশুও মারা যায়। বার্ষিক প্রাণহানির এই সংখ্যার বিচারে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। মৃত্যুর সংখ্যা বিচার করে সরকার ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বনাঞ্চল বৃদ্ধিসহ সরকার বিভিন্ন কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বজ্রপাতে মৃত্যু কমাতে আগাম সতর্কতা বা পূর্বাভাস দেওয়া এবং সচেতনতা বাড়াতে নিরলসভাবে কাজ করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম কালের কণ্ঠকে বলেন, “আমরা এখন গুরুত্ব দিচ্ছি আর্লি ওয়ার্নিংয়ে (আগাম সতর্কতায়)। এখন ১০ থেকে ১৫ মিনিট আগে বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। আর্লি ওয়ার্নিং যদি আমরা যথাযথ সময়ে দিতে পারি এবং এসএমএস বা ফোন কলের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করে দিতে পারি, তাহলে তা কাজে দেবে বলে মনে করি। সেই নিরিখেই কাজ হচ্ছে এখন। আধঘণ্টা আগেও বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। আধঘণ্টা মানে অনেক সময়। আধঘণ্টা আগে যদি আমরা পূর্বাভাস দিয়ে সতর্ক করতে পারি, তাহলে অনেক জীবন বাঁচানো সম্ভব। এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রথমবারের মতো বজ্রপাতের সতর্কবার্তা জারি করেছে চলতি বছরের ১৭ এপ্রিল। সেদিন প্রথম সতর্কবার্তায় দেশের ২৭ জেলার জন্য বজ্রপাত ও বজ্রবৃষ্টির সতর্কতা জারি করে অধিদপ্তর। এর পর থেকে নিয়মিত বজ্রপাতের আগাম সতর্কতা ও পূর্বাভাস দিয়ে আসছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। কিন্তু, বজ্রপাতের তথ্য বা সতর্কতা প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানোই সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। তাই, যেসব অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে, সেসব এলাকার মোবাইল টাওয়ার ব্যবহার করে মেসেজ বা ফোনকলের মাধ্যমে এলাকাবাসীকে সতর্ক করা যেতে পারে। বজ্রপাতে মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি রোধে আগাম সতর্কতা ও সচেতনতার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে আগাম সতর্কতা প্রদান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে গার্লস গাইড, বয়জ স্কাউট, রেড ক্রস, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কমিটির স্বেচ্ছাসেবীসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে কাজে লাগানো যায়। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বজ্রপাতসহ বিভিন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার কাজে সম্পৃক্ত করা গেলে সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত বজ্রপাতের তথ্য পৌঁছানো সম্ভব হবে। বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বজ্রপাতের সময় করণীয় সম্পর্কে সুপারিশমালা তৈরি করেছে। বজ্রপাতের সময় তা অনুসরণ করলে অনেক বিপদ থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। তাই, বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশমালা মানা খুব জরুরি।
এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রবৃষ্টি বেশি হয়; বজ্রপাতের সময়সীমা সাধারণত ৩০-৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করতে হবে। ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে ঘরের বাহিরে না যাওয়া; অতি জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে রবারের জুতা পড়ে বাইরে বের হওয়া। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ অথবা উঁচু স্থানে না থাকা। বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙ্গুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। টিনের চালা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। উঁচু গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার বা ধাতব খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে হবে। কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকতে হবে। বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতর অবস্থান করলে, গাড়ির ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ ঘটানো যাবে না; সম্ভব হলে গাড়িটি নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় থাকা যাবে না। জানালা বন্ধ রাখুন এবং ঘরের ভিতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকতে হবে। বজ্রপাতের সময় মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ল্যান্ডফোন, টিভি, ফ্রিজসহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এগুলো বন্ধ রাখতে হবে। বজ্রপাতের সময় ধাতব হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করা যাবে না। জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করতে হবে। বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখতে হবে এবং নিজেদেরও বিরত রাখতে হবে। বজ্রপাতের সময় ছাউনি বিহীন নৌকায় মাছ ধরতে যাওয়া যাবে না, তবে এ সময় সমুদ্র বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করতে হবে। প্রতিটি বিল্ডিং-এ বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে সরে যেতে হবে। কোনো বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে যেতে হবে। বজ্রপাতে কেউ আহত হলে বৈদ্যুতিক শকে আহতদের মতো করেই চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসককে ডাকতে হবে বা হাসপাতালে নিতে হবে। বজ্র আহত ব্যক্তির শাস-প্রশ্বাস ও হ্রদ স্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।
বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগের ক্ষেত্রে কিছু প্রস্তুতি নেবার সুযোগ থাকলেও বজ্রপাতের বিষয়টি অনেকটা ভূমিকম্পের মতোই আকস্মিক। কিন্তু আবহাওয়াবিদরা, রেডার ইমেজে মেঘের অবস্থান অনেক ওপরের দিকে দেখলে সেইসাথে বায়ুমণ্ডলে অস্থিতিশীল অবস্থা থাকলে দুই নম্বর সতর্ক সংকেত দিয়ে থাকেন। এমন অবস্থায় আকাশে কালো মেঘ ও বিদ্যুৎ চমকাতে দেখলেই সবাইকে সাথে সাথে খোলা জায়গা ছেড়ে দ্রুত নিরাপদে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। এসব পরামর্শ মেনে চললে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ থেকে নিরাপদে থাকা যাবে। বাড়ি-ঘর তৈরির সময় অবশ্যই আর্থিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোনো বাড়ি-ঘর বিদ্যুতায়িত হলে যাতে তা প্রাকৃতিকভাবেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। মৃত্যঝুঁকি কমিয়ে আনতে বজ্রপাত শেল্টারের পাশাপাশি বাড়াতে হবে লাইটনিং প্রটেস্ট সিস্টেম (এলপিএস) । বিভিন্ন স্থাপনাতে যদি এলপিএস লাগানো যায় এবং যদি এলাকাভিত্তিক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করা যায়, তাহলে বজ্রপাতের ঝুঁকি অনেক কমে যাবে। এছাড়া, সচেতনতা বৃদ্ধি, উন্নত পূর্বাভাস ব্যবস্থা এবং নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণও অত্যন্ত জরুরি। গাছ তার জীবন দিয়ে বজ্রপাত থেকে মানুষ ও অন্য প্রাণীর জীবন রক্ষা করে। ফলে এই মুহূর্তে আমাদের করণীয়, দ্রুত বর্ধনশীল গাছের চারা রোপণ করা। তাছাড়া, বজ্রপাত যেহেতু জলবায়ুসংক্রান্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু দূষণ প্রতিরোধ ও বৈশ্বিক তাপমাত্রা কমানোর ক্ষেত্রেও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, বিশ্বের সকল বিজ্ঞানীই একমত যে, জলবায়ু দূষণের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে গেছে। জলবায়ু দূষণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলোই বেশি দায়ী। বাংলাদেশসহ দরিদ্র দেশগুলোর দায় অনেক কম, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। কাজেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে বা একে মোকাবিলা করতে হলে সারাবিশ্বকেই একযোগে উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলো রক্ষার জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে সাহায্য দিতে হবে। ক্ষতিপূরণসহ আন্তর্জাতিক তহবিল সংগ্রহের জন্য সরকারকেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাছাড়া, সরকারকেও বজ্রপাতসহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে এবং প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত এ বরাদ্দের কার্যক্রম পৌঁছে দিতে হবে। তবেই, এর সুফল সবাই পাবে।
লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর
© ২০২৫ মেহেরপুর প্রতিদিন। সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত।