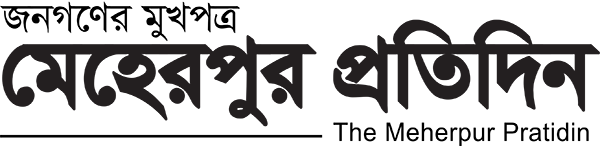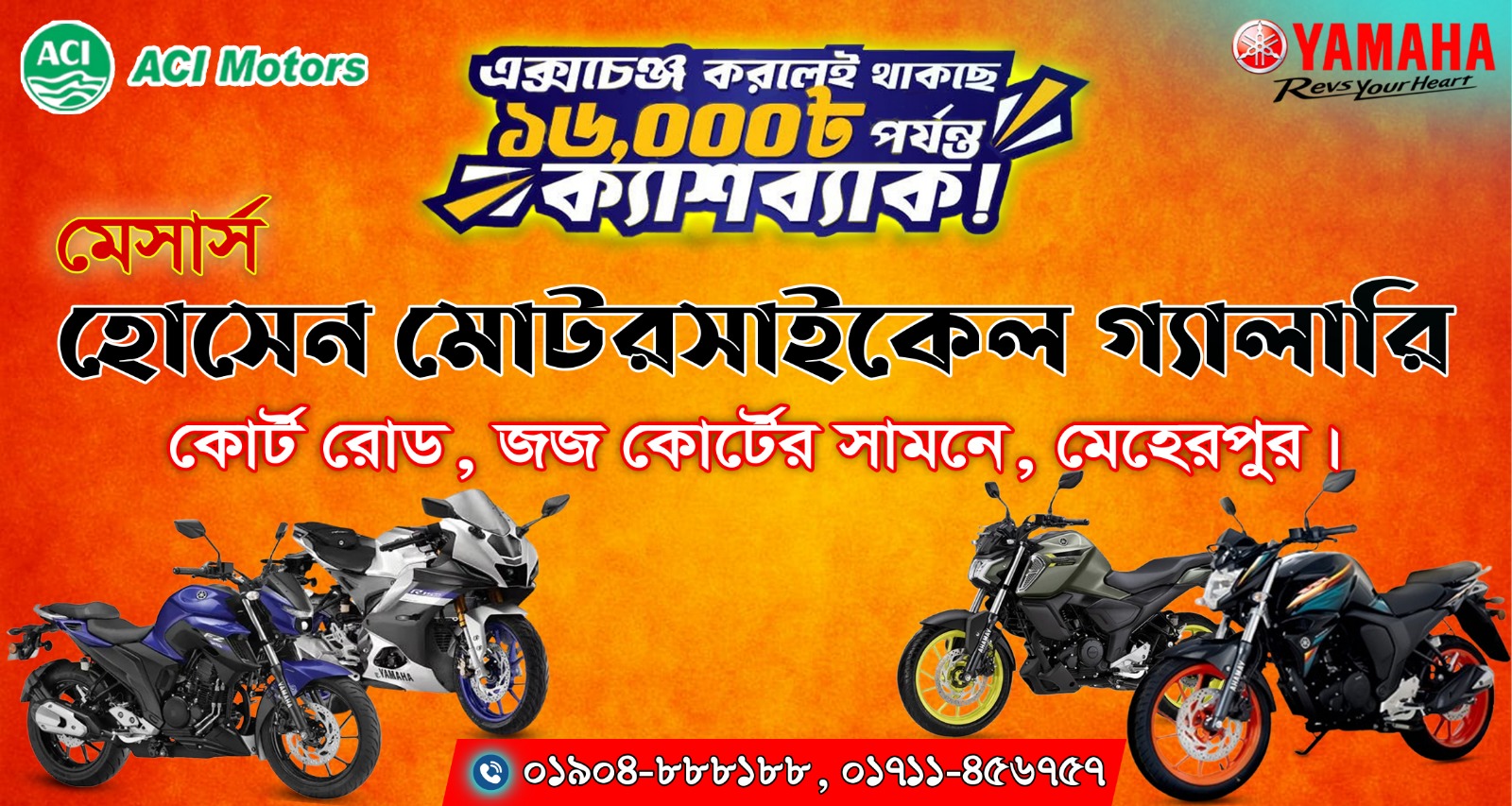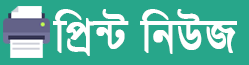
একসময় মেহেরপুর জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ছিল শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি আর আরতির আলো। আজ সেই দৃশ্য ক্রমে মিলিয়ে গেছে।
দেশভাগের আট দশক পেরিয়ে মেহেরপুর এখন প্রায় হিন্দুশূন্য জেলা হতে চলেছে- এমনটাই বলছেন স্থানীয় ইতিহাসবিদ ও সমাজ গবেষকেরা এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রতিবেদনে এমনটা দেখা যায়।
জেলা প্রশাসনের ও জেলা পরিসংখ্যান অফিসের তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে মেহেরপুরে মোট ২৫৯টি গ্রাম রয়েছে। এর মধ্যে ১৪৯টি গ্রাম এখন সম্পূর্ণ মুসলিম অধ্যুষিত। একটি হিন্দু পরিবারও নেই। ১৯৮১ সালের আদমশুমারিতে জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৪১ হাজার ৭২৭ জন, যার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ১.৬৪ শতাংশ।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), আদমশুমারি ১৯৮১, ২০১১ ও ২০২২, মেহেরপুর জেলা প্রশাসন, ২০২৪ সালের গ্রাম তালিকা অনুযায়ী, জেলার জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেলেও হিন্দু জনগোষ্ঠীর অংশ নেমে আসে ১.০৭ শতাংশে। অর্থাৎ, সংখ্যার হিসেবে তেমন পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু অনুপাতে হ্রাসটি উদ্বেগজনক। দেশভাগের পর থেকেই সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় মেহেরপুরের বহু হিন্দু পরিবার পাড়ি জমায় পশ্চিমবঙ্গে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও সেই ধারা অব্যাহত থাকে।
সদর উপজেলার উজ্জলপুর গ্রামে সনাতন ধর্মের মানুষের বসবাস ছিল ৮০ শতাংশ। দেশভাগের পর অন্নদা পন্ডিত ও প্রমথনাথ ছাড়া একে একে সকলেই পশ্চিম বাংলায় চলে যায়। অন্নদা পন্ডিতসহ পরিবারের সকলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে সর্বশেষ চলে যান প্রমথ নাথ। সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের শংকর বিশ্বাস বলেন- স্বাধনিতা পরবর্তীতেও আমাদের গ্রামে ত্রিশ-চল্লিশটি হিন্দু পরিবার ছিল, এখন গোটাতিনেক পরিবারের বসবাস। নাম প্রকাশে আপত্তি জানিয়ে একজন বলেন- ছেলেমেয়েরা সবাই ওপারে চলে গেছে। পৈত্রিক ভিটা আঁকড়ে আছি বুড়া-বুড়ি। তবে ওপারে গিয়ে ছেলে মেয়েরা ভালো নাই।
ইতিহাসবিদ আবদুল্লাহ আল আমিন জানান- দেশভাগের পর থেকে ৭১-এর যুদ্ধ, এরপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে মেহেরপুরের হিন্দু জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে প্রান্তিক হয়ে পড়ে। বিভিন্ন কারণে অনেকেই পারিবারিকভাবে ভারতে চলে যান।
শহর ও গ্রাম- উভয় স্থানেই এর প্রভাব স্পষ্ট। এক সময় মেহেরপুর শহরের বড়বাজার, কাঁঠালতলা, পাড়াগাঁও ও গাংনী বাজারে দুর্গাপূজা ও কালীপূজার জাঁকজমক থাকত। এখন সেই পূজামণ্ডপগুলোর অনেকগুলোই পরিত্যক্ত।
জমিদারী শাসনামলে মেহেরপরের জমিদার চন্দ্রগুপ্ত মল্লিক ও তার নায়েব এর বাড়িতে শারদীয় দুর্গা পূজা হতো প্রতিযোগিতা করে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবধরণের মানুষ সেই উৎসব উপভোগ করতো। এখন মল্লিক বাড়ির পূজা মন্ডপ ভগ্নদশা। ভগ্নপ্রা নায়েব বাড়ি সংস্কার করে সেখানে সনাতন ধর্মের মানুষ ২০১১ সাল থেকে শারদীয়া দূর্গোৎসব করে আসছে।
স্থানীয় পূজা উদ্যাপন পরিষদের আহবায়ক সনজিৎ পাল বাপ্পি বলেন- একটা সময় জেলা শহরে মল্লিক বাড়ি আর মূখার্জী পাড়ায় পূজা হতো। ১৯ শতক থেকে রাষ্ট্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় জেলায় ৪০ থেকে ৪৫টি স্থানে পূজা হলেও তাতে প্রাণ নাই হিন্দ পরিবার হ্রাস পাবার কারণে। ফলে সাংস্কৃতিক উৎসবের আবহ হারিয়ে গেছে। মন্দিরগুলো এখন শুধু স্মৃতিচিহ্ন। নতুন প্রজন্ম জানেই না- এই ঘরগুলোর ভেতরে একসময় ধর্মীয় গান, আলোকসজ্জা আর মিলনমেলার আয়োজন হতো।
গবেষকরা মনে করেন, জমিজমা হারানো, উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ রক্ষা নিয়ে জটিলতা, এবং পারিবারিক সংযোগের অভাব এই হ্রাসের অন্যতম কারণ। মেহেরপুরের এক সমাজবিজ্ঞানী বলেন- যখন একটি সম্প্রদায়ের সদস্যরা ক্রমাগত প্রবাসে চলে যায়, তখন তাদের সামাজিক শেকড় দুর্বল হয়ে পড়ে। একসময় পুরো গ্রামই খালি হয়ে যায়- এটিই ‘ডেমোগ্রাফিক সাইলেন্স’।
মেহেরপুর জেলা গঠনের আগে ও পরে এই অঞ্চল ছিল নদী ও ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র। ব্রিটিশ আমলেই এখানে হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত শ্রেণির আধিক্য ছিল। শহরের পুরোনো মহল্লাগুলোয় এখনো দেখা মেলে তাদের বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ, পাথরের গাঁথুনি, ধ্বসেপড়া বারান্দা, ভগ্ন মন্দির। দেশভাগের পর থেকে পশ্চিমবাংলা থেকে যেমন মুসলিমরা এপারে চলে আসতে শুরু করে। তেমনি সনাতন ধর্মের লোকজনও পশ্চিমবাংলায় চলে যাওয়া শুরু করে। এই যাওয়া আসা আর বন্ধ হচ্ছেনা।
সমাজকর্মীরা বলছেন, সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি না হলে এই ধারা থামানো যাবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সংগঠন ও প্রশাসনের উদ্যোগে সামাজিক সম্প্রীতির ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব।
মেহেরপুর কালি মন্দিরের এক তরুণ বললেনÑ আমরা এখানে আছি, থাকতে চাই। শুধু চাই নিরাপত্তা ও সমান সুযোগ।
একসময়ের হিন্দু অধ্যুষিত মেহেরপুর আজ পরিসংখ্যানের ক্ষুদ্র একটি শতাংশে সীমাবদ্ধ। অথচ এই জেলার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার সূচনাক্ষণÑ সবই ছিল ধর্মীয় সহাবস্থানের প্রতীক। সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া সেই চিত্র যদি ফিরিয়ে আনা না যায়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কেবল নামেই জানবে মেহেরপুরে কোনো একসময় হিন্দু গ্রাম ছিল।