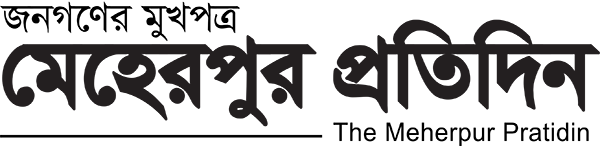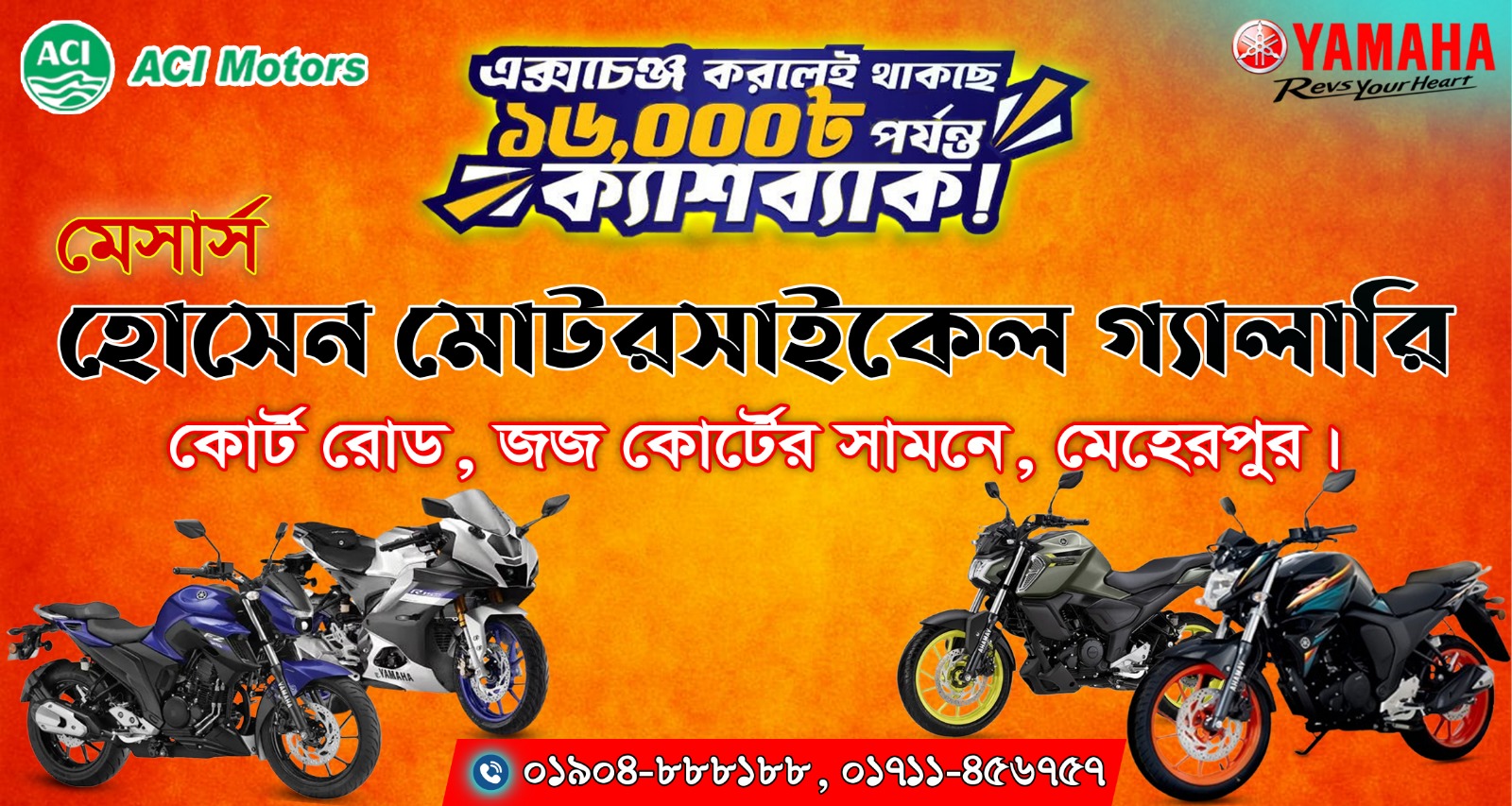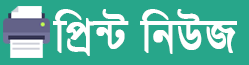
মানব সভ্যতার ইতিহাস আসলে সংগ্রামেরই ইতিহাস। ইতিহাসের ছোট বড় দাঙ্গা যুদ্ধ সবই এই সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। আর কথাসাহিত্যের কারবার যেহেতু মানুষ এবং মানুষের ছোট বড় সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম নানান বিষয় নিয়ে সেহেতু মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া এবং ঘটে চলা সংগ্রামের ইতিহাস ও কথাসাহিত্যে স্থান করে নেয় অনায়াসেই। বিশে^র সমস্ত দেশের কথাসাহিত্য সম্পর্কেই একথা সত্যি। বাংলা কথাসাহিত্য এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা কথাসাহিত্যের আদি থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত কথাসাহিত্যের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন দাঙ্গা ও আন্দোলন বারেবারে বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। তবে এখনো পর্যন্ত যে দাঙ্গাটি বাংলা কথাসাহিত্যকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে সেটি হল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মুহূর্তে দেশভাগকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গা এতটাই ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী ছিল যে লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই। এই দাঙ্গা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে খুব অল্প সময়েই তা ব্যক্তি মানুষের মনকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছে। এই দাঙ্গার অভিঘাত এতটাই সুদূরপ্রসারী ছিল যে দাঙ্গা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ব্যক্তি মানুষ তার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়নি। এই দাঙ্গা নারী, পুরুষ, শিশুসহ কেওই বাদ পড়েনি। ‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসে প্রফুল্ল রায় দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলাদেশের সময়ের এই চালচিত্রকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। সেই বিষাক্ত সময় একটি নারীর জীবনকেও কীভাবে বিষিয়ে দিয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয় কীভাবে এই দাঙ্গা ব্যক্তি নারীর জীবনে ট্রাজিক পরিণতি নিয়ে এসেছে ‘ কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসে প্রফুল্ল রায় তা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।
দেশভাগ এবং দেশভাগের অভিঘাত প্রফুল্ল রায়কে যে জীবন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছিল তা এতটাই গভীর ছিল যে সমগ্র জীবন তার প্রভাব থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেননি। মানুষের জীবনের সবথেকে সুন্দর সময় শৈশবের প্রায় পুরোটাই, ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কাটিয়েছেন পূর্ববঙ্গে। এরপর দেশভাগের ফলে উদ্বাস্ত হয়ে তাঁকে চলে আসতে হয় কলকাতায়। সে অভিজ্ঞতা মোটেই ভাল ছিল না। একবস্ত্রে পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায়। প্রতিমুহূর্তে ছিল খুন হয়ে যাওয়ার ভয়। পূর্ববঙ্গের একশ্রেণির মুসলমান তখন খুনের খেলায় মেতে উঠেছে। রাম দা নিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক মুসলমান প্রতিবেশী হিন্দুদের এই দুর্দিনে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এদের সহযোগিতায় অতি কষ্টে প্রথমে জাহাজে এবং পরে রিফুজি স্পেশাল ট্রেনে উদ্বাস্ত হিসেবে কলকাতায় প্রবেশ করেন তিনি। এরপর জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে। খুব কাছ থেকে দেখেছেন দাঙ্গার কারণে উদ্বাস্ত মানুষের জীবন যন্ত্রণা। এই গভীর জীবন অভিজ্ঞতা সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়কে বরাবরই চালিত করেছে। ‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসটি লেখকের গভীর জীবন অভিজ্ঞতার ফসল।
‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসে লেখক অনেকগুলি চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এই চরিত্রগুলি দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের ভয়াবহ পরিণতিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরে। ‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসে বিনু, ঝিনুক, যুগল, লারমোর প্রভৃতি চরিত্র, তাদের ক্রিয়াকলাপ এব তাদের পরিণতি তো দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষের চরম পরিণতিকেই মনে করিয়ে দেয়। যে বিনু পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে গিয়ে পূর্ববঙ্গের মাটিকে অন্তর দিয়ে ভালো ভেসে ফেলেছিল সেই বিনুকেই বিনা দোষে কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কাণে রাতের অন্ধকারে ব্যথাহত হৃদয়ে পালিয়ে চলে যেতে হল কলকাতায়। সত্যিই এই চিত্র মর্মান্তিক।
‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসে বহু চরিত্রের মধ্যেও আলাদা করে নজরে পড়ে ঝিনুক। বিনুর পাশাপাশি ঝিনুককে অত্যন্ত মমতা দিয়ে গড়ে তুলেছেন লেখক প্রথম থেকেই। ঝিনুক অভাগী। উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সবটা জুড়েই তার উপস্থিতি। উপন্যাস শেষ হয়েছে তার পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্যের মাধ্যমে। মানব সংসারে এরকম কিছু চরিত্র থাকে, যারা জন্ম থেকেই অভাগী। বিত্তের কারণে নয় সম্পূর্ণ ভাগ্যের দোষে ঝিনুক সেরকমই একটি চরিত্র। হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কীভাবে তার জীবনকে তিলে তিলে শেষ করে দিয়েছে তারই এক অনবদ্য ছবি অঙ্কিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। উপন্যাসের শুরুতে হেমনাথের সঙ্গে স্টিমার ঘাটে যখন ঝিনুককে প্রথম দেখা যায় তখন তার বয়স মাত্র আট।
“ছোট মেয়েটির চুল কোঁকড়া। নাকটি একটু বোঁচাই হবে। ফুলো
ফুলো নরম লালচে গাল। রূপোর কাজল লতার মতো চোখের কালো
মণি দু’টো টলটল করেছে। একটু নাড়া দিলেই টুপ করে ঝরে পড়বে। নীল
ফ্রক লাল জুতোয়, মনে হয়, মোমের পুতুলটি”১
এই নিষ্পাপ কোমল পবিত্র ছোট্ট মেয়েটি তখনও জানে না যে কি ভীষণ দুঃখের ইতিহাস রচিত হতে চলেছে তার জীবনে। বাবা-মায়ের দাম্পত্য জীবনের মিলহীনতার খেসারত দিতে হয়েছে এই ছোট্ট মেয়েটিকে। ঝিনুকের মা অন্য কিছুর প্রতি প্রবল আকর্ষণে শুধু স্বামী ভবতোষকে ছেড়ে যায়নি, ছেড়ে চলে গেছে দুধের শিশু ঝিনুককেও। অভিব্যক্তি শুধু চোখে জল এনে দেয় না, হৃদয়কেও ভারাক্রান্ত করে তোলে। এরপর যখন ভবতোষ ও স্নেহলতার কথোপকথন আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে শুনে নিয়েছে তখন ঝিনুক সত্যিই জেনে গেছে যে তার মা আর ফিরবে না। তখন ছোট্ট ঝিনুকের কান্না পাঠককেও কান্নায় ভাসিয়ে দেয়।
ঝিনুকের জীবনের দুঃখের অধ্যায় এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। ঝিনুক তখনো জানতো না যে কি ভয়ানক দুঃখ তার জন্য অপেক্ষা করে আছ্।ে দেশভাগের পর সারা পূর্ব বাংলা জুড়ে শুরু হওয়া সাম্প্রাদিয়ক দাঙ্গার সময় অসুস্থ মাকে দেখতে ঝিনুক বাবা ভবতোষের সঙ্গে ঢাকায় রওনা দিয়েছে। সেখানে গিয়ে তারা ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক
দাঙ্গার মধ্যে পড়েছে। ভবতোষকে সেখানে খুন হতে হয়েছে। আর তাকে হতে হয়েছে ধর্ষিতা। ধর্ষিতা ঝিনুককে উদ্ধার করে নিয়ে বাড়ী ফিরে এসে হেমনাথ সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেছে স্নেহলতাকে:
“…. এখান থেকে ঢাকা পৌঁছবার পর ভবতোষ দাঙ্গার ভেতর পড়ছিলেন। ঘাতকের দল ভবতোষকে মেরে ফেলেছে। তারপর ঝিনুককে নিয়ে চলে গিয়েছিল। হেমনাথ ঢাকায় গিয়ে পুলিশ দিয়ে ঝিনুককে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু ভবতোষের মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায়নি।
শ^াপদেরা ষোল সতের দিন একটা বাড়িতে ঝিনুককে আটকে রেখেছিল। যে অবস্থার তাকে উদ্ধার করা হয়েছে, তার চাইতে সে যদি মরে যেত!”২
এরপর ঝিনুক প্রায় অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যায়। অপ্রকৃতিস্থ ঝিনুককে নিয়ে বিনু পাড়ি দেয় কলকাতায়। বিনুর বিশ^াস ছিল ঘনিষ্ঠজনেরা দুহাত বাড়িয়ে ঝিনুককে বুকে জড়িয়ে নেবে। জীবনের দগদগে ক্ষত স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগিয়ে জুড়িয়ে দেবে। যাবতীয় যন্ত্রণা, ভুলিয়ে দেবে সেদিনের যত মর্মান্তিক স্মৃতি। কিন্তু ঝিনুকের অদৃষ্ট তেমন নয়। সেখানে হেমনলিনী মানে তার জামাই বাবু আনন্দের মা তাকে মুখের ওপর স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে:
“দেখ মা, তোমাকে আমি এমন একটা কথা বলব যাতে দুঃখ পাবে, কিন্তু না বলেও পারছি না। শুনেছি ঢাকায় গিয়ে তুমি রায়টের মধ্যে পড়েছিলে। গুন্ডারা ক’দিন তোমাকে আটকে রেখেছিল। খবরটা শোনার পর খুব কষ্ট হয়েছিল। জানি তোমার কোন অপরাধ নেই, তুমি নির্দোষ। কিন্তু আমি পুরনো দিনের মানুষ। নানা সংস্কারে আটকে আছি। এই বয়েসে সেসব কাটানো সম্ভব নয়। একটু থেমে বললেন, ‘যে ক’দিন আছ, এক তলাতেই থাকবে। দোতলায় আমাদের ঠাকুর ঘর। তুমি ওপরে না উঠলেই ভাল হয়।”৩
এখানেও ধর্ষিত হতে হয়েছে ঝিনুককে। শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবে। তবু এই জগত সংসারে তার একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল বিনু। বিনুই তাকে শত ঝড় জল আঘাত থেকে রক্ষা করেছে। ঝিনুকের হয়তো ভরসা ছিল বিনুর পিতা অবনীমোহনের প্রতিও। কাশী থেকে ফিরে এসে বিনু ও তাঁর পিতা অবনীমোহনের কথোপকথন জীবনের সবচাইতে কঠিন বাস্তবের সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে:
“তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকারী কথা আছে। সেটা তোমাকেই শুধু
বলতে চাই। ঝিনুক, তুমি পাশের ঘরে যাও।
ওখানে খাট বিছানা চেয়ার টেয়ার সবই আছে।
নত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ঝিনুক। অবনীমোহন সোজাসুজি ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন- ‘ঝিনুকের খবরটা অনেক আগেই আমি পেয়েছি। ভীষণ দুঃখজনক ঘটনা। শুনে খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু–’৪ক
অবনীমোহন বলে যেতে লাগলেন: “ঝিনুককে যে পাকিস্তান থেকে আনলে, ওকে নিয়ে কি করবে ভেবেছ? ঠিক এই ধরণের প্রশ্ন সেদিন ঝুমাও করেছিল। বিনুর বুকের ভেতরটা আমূল কেঁপে যায়। সে উত্তর দেয় না।” ৪খ
অবনীমোহন বলে যান: “ কোনও আত্মীয়-স্বজন এমন মেয়েকে শেল্টার দেবে কিনা সন্দেহ। তুমি যদি আলাদা বাড়ি ভাড়া করে ওকে নিজের কাছে রাখতে চাও, হাজারটা প্রশ্ন উঠবে। লোকে জানতে চাইবে মেয়েটা কে। তোমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। কী জবাব দেবে তখন? শুধু একটা পথ খোলা আছে–’
আবছা গলায় বিনু জিজ্ঞেস করল, ‘কি?’
‘যদি তুমি ওকে বিয়ে কর, সমস্যাটা মিটতে পারে। কিন্তু আত্মীয়রা তোমাদের ত্যাগ করবে। তা ছাড়া, এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করার সাহস কি তোমার আছে?”৪গ
পিতার মুখ থেকে এই কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল বিনুর। অনেক কথাই তখন মনে হল তার। বিষবাষ্পে-ভরা পূর্ব বাংলা থেকে কী নিদারুণ আতঙ্কের মধ্যে ঝিনুককে সীমান্তের এপারে নিয়ে এসেছে, তা শুধু সে-ই জানে। কিন্তু অবনীমোহন তাকে জীবনের সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে দুরূহ সংকটের সামনে দাঁড় করিয় দিয়েছেন। বিপন্ন, দ্বিধাগ্রস্থ, শ^াসরুদ্ধ বিনু কী জবাব দেবে, ভেবে পেল না। অবনীমোহন বললেন:
“একটা কথা ভেবে দেখতে পার। এ জাতীয় মেয়েদের জন্য গভর্নমেন্টের হোম আছে।
সেখানে আপাতত ঝিনুককে রাখা যেতে পারে।’
বিনু তখন কথা বলার অবস্থায় ছিল না। অবনীমোহন বলে যেতে থাকেন:
‘তুমি ঝিনুকের কাছে যাও।’ এক্ষুনি নয়, সময় নিয়ে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ‘হোম’-এর
ব্যাপারটা বোলো।’
শরীর এবং মন কঠিন আঘাতে অসাড় হয়ে গেছে। নিজেকে ধীরে ধীরে টেনে তুলল বিনু। পাশের ঘরে এসে দেখল, সেটা একেবারে ফাঁকা। সে ডাকতে লাগল, ‘ঝিনুক–ঝিনুক–’ সাড়া নেই।
তেতলার অন্য ঘরগুলো আতিপাতি করে খুঁজল বিনু। কোথাও ঝিনুককে পাওয়া গেল না। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে দোতলায়, তারপর একতলায় নেমে এলো সে। ঝিনুক কোথাও নেই।” ৪ঘ
ঝিনুকের জীবনের এই পরিণতি মেনে নিতে কষ্ট হয়। তার এই পরিণতি কোনমতেই প্রত্যাশিত ছিল না। ঝিনুকের তো কোন দোষ ছিল না। সে তো দাঙ্গাবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অস্থির সময়ের শিকার। কোনভাবেই যেন এর থেকে তার নিস্তার নেই। শুধু ঝিনুকই নয় তার মতো হাজার হাজার নারীকে বাংলাদেশের দাঙ্গা বিধ্বস্ত সেই উত্তাল সময়ে এই নারকীয় যন্ত্রণার শিকার হতে হয়েছে। ইতিহাস বইয়ের পাতায় দু একটি শব্দের খোঁচায় হয়তো বা তার ইতিহাস তুলে রাখা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের নারীর জীবনে ঘটে যাওয়া সেই যন্ত্রণাময় ইতিহাস জীবন্ত হয়ে আছে সাহিত্যের পাতায়। যে সমস্ত সাহিত্যিক এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রফুল্ল রায়। তাঁর ‘কেয়া পাতার নৌকা’ উপন্যাসের ঝিনুক দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলাদেশের হাজার হাজার ত্রস্ত নারীর প্রতিনিধি।
লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ^বিদ্যালয়