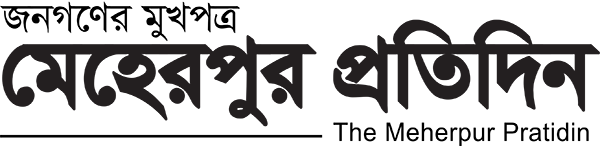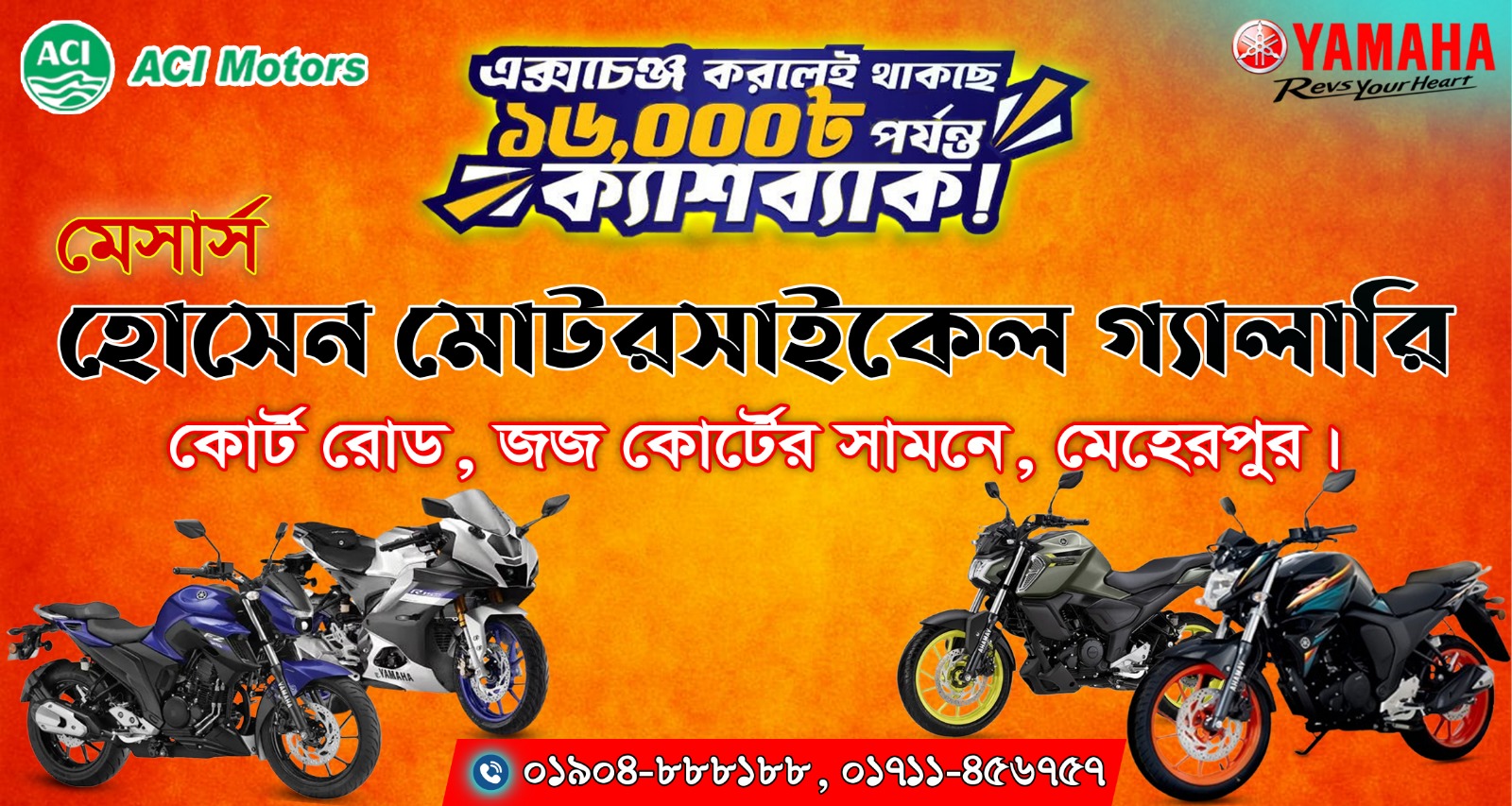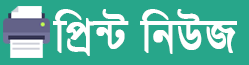
দেশের রাজনৈতিক পরিসর এক আশ্চর্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের চর্চা, মত প্রকাশের অধিকার ও জনগণের অংশগ্রহণ এখন অনেকটাই প্রতীকী। এর পরিবর্তে সামনে এসেছে এমন একটি বাস্তবতা, যেখানে রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে একটি বিশেষ শ্রেণি “রাজনীতির শ্রমিক”। এরা আদর্শের নয়, আনুগত্যের ভিত্তিতে রাজনীতিতে সক্রিয়; এবং তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকা অধিকাংশ সময়েই সীমাবদ্ধ থাকে ক্ষমতার পক্ষে শ্রম প্রদান ও প্রতিপক্ষ দমনে সক্রিয় অংশগ্রহণে।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন নেতৃত্বের সংকট এখন গভীর বাস্তবতা। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশের রাজনীতিতে বেশ কয়েকটি প্রজন্ম নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এক ধরনের স্থবিরতা লক্ষণীয় নেতৃত্ব কাঠামো পুরোনো, মুখ একই, কণ্ঠস্বরও চেনা। প্রশ্ন উঠছে: আজকের তরুণেরা কোথায়? ভবিষ্যতের নেতৃত্ব কোথা থেকে আসবে?
এক সময়ের ছাত্র রাজনীতি ছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মূল প্ল্যাটফর্ম। আজ তা অনেক ক্ষেত্রেই সহিংসতা, চাঁদাবাজি ও দলীয় আজ্ঞাবহতায় পরিণত হয়েছে। আদর্শিক রাজনীতির জায়গায় এসেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপার্জনের চিন্তা। ফলে তরুণদের মধ্যে রাজনীতিকে ক্যারিয়ার হিসেবে দেখার আগ্রহ কমে গেছে। যেসব তরুণ এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারাও বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছেন।
শেখ হাসিনা দীর্ঘ সময় ধরে শাসন ব্যবস্থায় থাকার ফলে মাঠপর্যায়ে এক ধরনের ‘দলভিত্তিক শ্রম বাজার” গড়ে উঠেছে। এখানে রাজনীতিকরা আদর্শিক বক্তব্য দেন না; বরং নেতা কী বলছেন, তা অন্ধভাবে অনুসরণ করাই যেন একমাত্র কাজ। শোডাউন, মিছিল, পোস্টার লাগানো, এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার চালানো পর্যন্ত সবই এখন একপ্রকার পেশা, যার বিনিময়ে পাওয়া যায় পদ, সুযোগ বা সরাসরি আর্থিক সুবিধা।
এই ধরনের রাজনীতি শ্রমিকদের কাছে রাজনীতি হলো লেনদেনের মাধ্যম আদর্শ নয়, বরং সুবিধার সূত্র।
বিরোধী রাজনীতির শ্রমিক সংকট। ওইসময়, বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপি ও বাম ধারার দলগুলো রাজপথে সক্রিয় শ্রমিক-কর্মী হারিয়ে ফেলে। কোটা বিরোধী আন্দোলনে কেষ হাসিনা সরকারের পতনের পরে সেই সংকট কাটিয়ে ওঠে বিএনপি। এখন বিএনপিতে রাজনীতির শ্রমিকে জয় জয়কার। এখানে আদর্শে বিশ্বাসী কিছু মানুষ এখনও আছেন, তবে তাঁদের সক্রিয়তা তুলনামূলকভাবে কম।
এ বাস্তবতায় দেখা যায়, শ্রমিক-কেন্দ্রিক রাজনীতি শুধু ক্ষমতাসীন পক্ষেই নয়, বিরোধীতায়ও এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি করে।
বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতি একসময় ছিল চিন্তার মঞ্চ, নেতৃত্ব গড়ার প্ল্যাটফর্ম। আজ তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রূপ নিয়েছে সংঘবদ্ধ পেশাগত কর্মকাণ্ডে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্র সংগঠনের নামে চলে টর্চার সেল, চাঁদাবাজি, নিয়ন্ত্রণের লড়াই। ছাত্ররা শিক্ষার্থী নয়, বরং নেতা ও উপরের মহলের ‘বিশ্বাসভাজন কর্মী’ হয়ে ওঠে এবং সেটাই তাদের “রাজনৈতিক যোগ্যতা”। তাদের মধ্যে অনেকে বছরের পর বছর ছাত্রত্ব বজায় রেখে রাজনীতি করে চলেন একটা ‘ক্যাডার সংস্কৃতি’র প্রতিনিধিত্ব করেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনীতির এক নতুন মঞ্চ তৈরি হয়। যেখানে রাজনৈতিক শ্রমিকরা ফেসবুক পোস্ট, ইউটিউব লাইভ, বা ভিডিও কনটেন্টের মাধ্যমে ‘নেতার পক্ষে’ কথা বলেন, বিরোধী মতকে আক্রমণ করেন। তাঁদের অনেকেই এই কাজের বিনিময়ে আর্থিক উপার্জন বা সুযোগ সুবিধা পান।
এটি একধরনের “ডিজিটাল দালালি”, যা মূলত রাজনীতিকে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা থেকে সরিয়ে এনে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচারণার যন্ত্রে পরিণত হয়ে ওঠে। এখনও এই চর্চা চলমান।
রাজনীতির এই শ্রমিকতন্ত্র কেবল দলীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। নিয়োগ, বদলি, উন্নয়ন প্রকল্প, এমনকি পুলিশের মামলাতেও দলীয় পরিচয় নির্ধারণ করে দেয় কে ‘অপরাধী’ আর কে ‘ভিকটিম’। রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই সংস্কৃতি যদি চলতেই থাকে, তবে রাজনীতি কেবলই ক্ষমতা রক্ষার উপকরণে পরিণত হবে। গণতন্ত্র থাকবে শুধু ভোটের দিনটিতে, আর বাকিটা সময় থাকবে নির্দিষ্ট দলের মুখপাত্রদের হাতে যাঁরা আদর্শ নয়, নির্দেশ পালন করতেই উৎসাহী।
সেই দায় দলগুলোর যেমন, তেমনি সমাজ ও নাগরিকদেরও। এখনই সময় প্রশ্ন তোলার, জবাব চাওয়ার, এবং নতুন এক রাজনীতি কল্পনার। যেখানে মানুষ হবে রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র্র, আর রাজনীতি হবে মত, বিবেক ও মূল্যবোধের জায়গা শ্রম বিক্রির নয়।
দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে গণতন্ত্রের অভাব যেমন নতুন নেতৃত্ব ঠেকিয়ে রাখে, তেমনি জাতীয় রাজনীতিতে বিরোধী মতকে দমন করার প্রবণতা রাজনীতিকে একমাত্রিক করে তোলে। ভিন্নমতের বিকাশ না থাকলে নেতৃত্বের বিকাশও থেমে যায়।
নতুন নেতৃত্ব গড়তে হলে- দলীয় নেতৃত্বে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে। নেতৃত্ব নির্বাচন হতে হবে ভোটের মাধ্যমে, নিযুক্তির মাধ্যমে নয়।
ছাত্র রাজনীতিকে আদর্শভিত্তিক ও শিক্ষাবান্ধব করতে হবে। ক্যাম্পাসে নিয়মিত ও নিরপেক্ষ ছাত্র সংসদ নির্বাচন চালু করা জরুরি।
নতুন নেতৃত্বের জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে। মিডিয়া, সেমিনার, গবেষণা ও নীতি আলোচনা সভায় তরুণদের অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে হবে।
রাজনীতিকে পেশাগতভাবে সম্মানজনক করতে হবে। দুর্নীতি ও সহিংসতা থেকে মুক্ত করে এটিকে আকর্ষণীয় ও নৈতিক জায়গায় ফিরিয়ে আনা দরকার।
বিরোধী মতের প্রতি সহনশীলতা বাড়াতে হবে। গণতন্ত্র মানে শুধু নির্বাচন নয়, বরং প্রতিটি স্তরে ভিন্নমতের সহাবস্থান। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বড় একটি অংশ তরুণ। এরা যদি রাজনীতির বাইরেই থাকে, তাহলে নেতৃত্বের সংকট কেবল আরও গভীর হবে। রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একসঙ্গে কাজ করে নেতৃত্ব তৈরির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যতের রাজনীতি যেন কিছু মুখ বা পরিবারের হাতে না আটকে থাকে, বরং হয়ে ওঠে জনসম্পৃক্ত, দায়বদ্ধ এবং নবীন নেতৃত্বনির্ভর সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।
লেখক ও সাংবাদিক